চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্র ছোটগল্পে অন্ত্যজ- ভাবনা
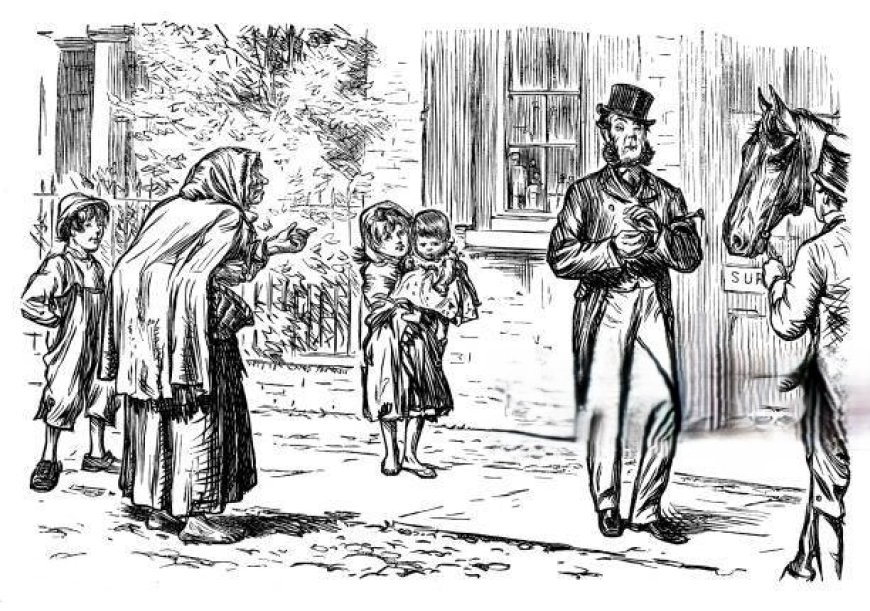
চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্র ছোটগল্পে অন্ত্যজ- ভাবনা
নিম্নবর্গ বা অন্ত্যজ শব্দের আভিধানিক অর্থ অন্তিমে যার ঠাঁই। কথাটিকে সোজা করে বললে নিচুজাতি। ইংরেজিতে (Subaltern) শব্দটি সামরিক ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়ে থাকে। সাধারণ ধারণায় এগিয়ে গেলে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় নিম্নস্থিত হিসেবে। ঐতিহাসিকভাবে অসম বিকাশ সূত্রে শব্দটি নিম্নবর্গের অভিধায় অভিষিক্ত। সামন্ততান্ত্রিক বিবেচনায় সামাজিকভাবে নিপীড়িত, জাতিবৈষম্যে অত্যাচারিত, ধর্মীয় নির্যাতন ও শিক্ষার আলো বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষেরই প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ। অন্যদিকে মনুসংহিতার প্রতিটি নিয়ম হিন্দু সম্প্রদায়ের সংবিধান।
মনুবাদ মতে ‘অব্রাহ্মণরাই শুদ্র।’ বিষয়টি স্পষ্ট করতে রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন, নাটকের পুরোহিত ‘রঘুপতি গোবিন্দ’-‘মাণিক্যকে শুদ্র’ বলে সম্ভাষণ করেছেন। ‘আমি বিপ্র, তুমি শুদ্র।’ বাংলায় এই নিম্নবর্গের অতি নিকট অনেক প্রতিশব্দ নজরে পড়ে- প্রান্তিক, ওরা ও দলিত প্রভৃতি নামে। বুর্জোয়া সমাজে,‘সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাসকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গ ধারণা আলোচিত হয়।’১ প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল বেশিরভাগ মানুষকে ‘শুদ্র’ বলে পরিচিতি পেত। বৈদিক যুগ পেরিয়ে মনুসংহিতার আইনে এ শ্রেণীভেদ আরো কঠোর হয়ে ওঠে। সামাজিক মানুষ হিসেবে এ নিম্নবর্গীয় মানুষেরা শাসনের কৌশল ও ধর্মের নীতির কারণে পদদলিত হয়েছে বারংবার।
শাসকদের কাছে তাই তারা অচ্যুত মানুষ হিসেবে নিগৃহীত হয়েছে। সৃষ্টিশীল লেখকরা সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে তাদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন অনায়াসেই। বাংলা ভাষার প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদে প্রথম দেখতে পাওয়া যায় নিম্নবর্গ মানুষকে। এক পদকর্তা লেখেন,‘ছৈ ছৈ জাইসে ব্রাহ্মণ নাড়িয়া।’ অতঃপর মঙ্গলকাব্যেও তাদের বিচরণ বেশ বিস্তৃত। সময়ের প্রবাহে উপন্যাস,গল্প ও নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয়ভূষণ মজুমদারের হাত হয়ে চলছে অবিরাম।
রবীন্দ্রনাথ রচিত সাহিত্যের অন্যতম দিক ছোটগল্প। যুগের নানা চৈতন্য তথা মানব সমস্যার টানাপড়েন তাঁর গল্পগুলোতে প্রতিফলিত। সে পথ ধরে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে অন্ত্যজন তথা প্রান্তিক মানুষের শোষণ ও অত্যাচারের কথা রেখায়িত হয়েছে নিপুণভাবে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনেছিলেন দেশের সাধারণ মানুষের দুরবস্থার উৎস। যুগে যুগে শাসকদের শোষণের বাহারি কৌশল মানুষের দরিদ্রতার অন্যতম কারণ। সে সময়ে বৃহৎ ভারতবর্ষ বর্ণভেদ ও ধর্মীয় কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সমাজব্যবস্থা ভেঙে পিছিয়ে থাকা শ্রমজীবী ও নিরন্ন মানুষকে আলোকিত করে,মানবতাবাদের এক নতুন ভারত প্রত্যাশা করেছেন।
বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের সকল দুর্বিপাকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রান্তিকজনের মানবিক আত্মীয়। আস্তিক ভাবনায় স্থির এ কবি ধর্মীয় উন্মাদনা ও ব্রাহ্মণপ্রথার প্রতি স্পষ্ট ঘৃণা পোষণ করতেন। এদিক থেকে বৌদ্ধধর্মের মানবতা এবং শাশ্বত মানব ধর্মের ঝান্ডাকে তিনি সতত বহন করেছেন। আপন ভাবনার এই আলোকিত উঠান থেকেই তিনি নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা অনুভব করেছেন। ফলে তাঁর প্রতিটি ছোটগল্পে মানবতার মুগ্ধতা বাস্তবতার অঙ্গীকারে গভীরভাবে ছড়িয়ে আছে। দেনা-পাওনা (১২৯৮) গল্পটি সমাজের ঘৃণিত পণ-প্রথার উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে। সোমত্ত মেয়েকে কেন্দ্র করে একজন গরীব পিতার অসহায়তা গল্পের প্লটকে নিবিড় ঘন করেছে। শাস্ত্রশিক্ষা, নীতি-শিক্ষার প্রতীক শোষক রায়বাহাদুরের লোভের কাছে হার মেনেছে মানবতা, শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব। গল্পের ভেতর করুণ ছবি দুই দিক থেকে প্রতিভাত হয়েছে। এক. পিতা রামসুন্দরের অপত্য স্নেহের মৃত্যু। এবং দুই. একই সঙ্গে কন্যা নিরুপমার শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ।
মুক্তির উপায় (১২৯৮)পারিবারিক জীবনের নির্মম ছবি এখানে চিত্রিত। নিরীহ ফকির চাঁদ সংসার ধর্ম পালনে অপারগ হয়ে পরিবার ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়। আর্থিক অসচ্ছলতা বাঙ্গালী জীবনকে কতখানি হীন করে সেই ছবি ফকির চাঁদ চরিত্রের ভেতর দিয়ে শিল্পীত করেছেন গল্পকার। প্রান্তিক মানুষের জায়গা পথে পথে গল্পটিতে এই দৃশ্য স্পষ্ট হয়েছে। পোস্টমাস্টার (১২৯৮) রতন ও পোস্টমাস্টারের জীবনের অসম পার্থক্যের সঙ্গে অনাথ রতনের অসহায়তা এ গল্পের উজ্জ্বল প্রান্ত। গ্রামীণ জীবনের কষ্ট শহুরে পোস্টমাস্টার অজ পল্লীতে এসে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। চাকরির নিয়মে একদিন পোস্টমাস্টার কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেছে, কিন্তু পিছনে রেখে গেছে পতিত অসহায় রতনকে। গল্পের শেষ ছবি কালোত্তীর্ণ হয়েছে পোস্টমাস্টারের দার্শনিক সুলভ সেই চিরন্ত শেষ বাক্যটির মধ্যে,-‘পৃথিবীতে কে কাহার?’ অন্তজ রতন আসলেই কারো নয় এ পৃথিবীতে।
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন (১২৯৮) দারিদ্র্য অসহায় মানুষের করুণ ছবি এ গল্পটি। প্রান্তিক মানুষ রাইচরণ অনুকূল বাবুদের দুই পুরুষের চাকর। এই রাইচরণের কোলে-পিঠে বড় হয়েছে অনুকূল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস অনুকূলের ছেলেকে কদম ফুল এনে দিতে গিয়ে সব হারিয়ে গেছে রাইচরণের। নিজের বুকের ধনকে বিসর্জন দিয়ে তার রক্ষা মিলেছে। কিন্তু ‘মনে রাখতে হবে রাইচরণের এ মনন প্রভুর প্রতি ভৃত্যের নিঃশর্ত আত্মনিবেদন এবং কৃতঘ্নতাহীন বিশ্বস্ততার ফল।’২ ত্যাগ (১২৯৮) জাত ধর্মের কাছে মানবিকতা ও প্রীতির কোনো মূল্য নেই এটি গল্পের মূল পরিপ্রেক্ষিতে। বসন্ত সমীরণের প্রলেপ ভিজানো রাতে স্ত্রী কুসুমকে নিয়ে অনুরাগে মগ্ন হেমন্ত। ঠিক সেই ক্ষণে ব্রাহ্মণবাদের ধারক পিতা হরিহর মুখুর্জ্জে বজ্রকন্ঠে শাসিয়ে ওঠেন- ‘হেমন্ত বউকে এখনই বাড়ি থেকে দূর করিয়া দাও।’
কুসুমের পূর্ব বিবাহ সংবাদ মুখুর্জ্জে মশায় সবেমাত্র পেয়ে অগ্নি শর্মা হয়ে যান। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা জানার পর হেমন্ত স্ত্রী কুসুমকে ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালে, পিতা মুখুর্জ্জে বলে ওঠে,‘তবে তুইসুদ্ধ দূর হইয়া যা।’ মুসলমানির গল্প (১৯৪১) জাত-পাতের ঊর্ধ্বে মানব ধর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে এ আখ্যানে। একজন প্রকৃত মুসলমান উদারতা ও মানবধর্মে কতখানি উজ্জ্বল সেই ছবি এখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিক্ষুব্ধ সময়ে বংশী বদনের ঘরে কন্যা কমলার জন্ম হয়। মাতা-পিতার মৃত্যু হলে কাকার কাছে মানুষ হয় কমলা। কিন্তু কাকী কমলাকে বিদায় করতে শেঠ বংশের স্বভাব মাতাল মেজোছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন। বরযাত্রী বউকে নিয়ে যাবার প্রাক্কালে ডাকাতের কবলে পড়ে। ঠিক এ সময়ে বৃদ্ধ মুসলমান হবির খাঁন কমলাকে উদ্ধার করে মা ডেকে বাড়িতে জায়গা দেন। কমলা বড় হলে হবির খাঁর বদান্যতায় নিজ কাকার কাছে ফিরে যায়। কিন্তু কাকী পুনরায় তাকে তাড়িয়ে দেন। অবশেষে খাঁন সাহেবের বাড়িতেই শেষ আশ্রয় পায় কমলা। মানবধর্মের জোছনায় ভরে উঠেছে এ গল্পের ভেতর বাহির। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গল্পের উপাদান হয়ে আছে নিম্নবর্গের সহায়হীন মানব-মানবী। অস্পৃশ্যদের অধিকারের দিকটি রবীন্দ্র গল্পগুলোর আলোকিত অধ্যায়। শাস্তি গল্পে অন্ত্যজ মানুষের করুণ পরিণতিকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন পরম মমতায়।
১৯৪৭ স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের জাতীয় জীবন ছিল বিপন্ন। ইংরেজ শোষক ও দেশীয় অত্যাচারীদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে আসে সীমাহীন দুর্বিপাক। ঠিক সে সময়ে একজন মানবতাবাদী দায়বদ্ধ লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প, উপন্যাস ও নাটকে মানব মুক্তির দিকটিকে শিল্প-প্রকরণে উদ্ভাসিত করেছেন। যা তাঁকে একজন অসামান্য শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে বিশ্ব দরবারে। মানব প্রেমিক বিশ্বকবি তাই তো বলতে পেরেছেন- ‘মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক। আমি তোমাদেরি লোক, আর কিছু নয়, এই হোক মোর শেষ পরিচয়।’ (সংক্ষেপিত)
তথ্যসূত্র :
১. ড. মামুন অর রশীদ, বাংলা উপন্যসে নিম্নবর্গ,শুদ্ধস্বর-ঢাকা ২০১৪
২. ড. হারুন-অর-রশীদ, রবীন্দ্রসাহিত্যে মানব সম্পর্ক প্রসঙ্গ গল্প, শোভা প্রকাশ ২০০৪



